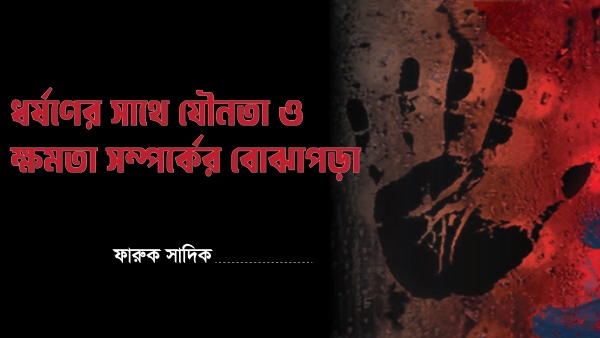এই সময়ে সেন্সেটিভ এবং সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে যে বিষয়টা, তা হচ্ছে ধর্ষণ। ব্যাপারগুলো নিয়ে নানান পক্ষ নানান ভাবে নানান ধরণের মতামত দিচ্ছেন। ফলে একটা রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলনে মানুষজন বিভিন্ন ধরনের দাবি করতেছেন। এই যে ধর্ষণের বিচার সংক্রান্ত দাবীগুলো আপনারা শুনতে বা দেখতে পারতেছেন, এই ব্যপারগুলোয় আসলে গোড়ায় সমস্যা আছে। ফলে আমার কাছে যেইটা মনে হইছে, পুরা দেশের মধ্যে আমাদের সাধারণ যে চিন্তা-ভাবনা, সেখানে বোঝাপড়ায় একটু ঝামেলা আছে। বোঝাপড়ায় ঝামেলা কীরকম? ধর্ষণ জিনিসটাকে আপনি কীভাবে দেখেন, এটা আসলে কী, ধর্ষণ কোন যৌনতার ফর্ম কি-না, ধর্ষণের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রের কী অবস্থান বা আইনগুলোর কী ব্যাপার-স্যাপার ইত্যাদি !
প্রথমত, ধর্ষণ ব্যাপারটা আসলে কোন যৌনতার ফর্ম না। ধর্ষণের সাথে আমাদের যৌনাঙ্গ/সেক্সচুয়াল অর্গানগুলো রিলেটেড, সেক্সচুয়াল অর্গানগুলোর মাধ্যমেই ধর্ষণগুলো ঘটে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু সেক্সচুয়াল অর্গানগুলোর মাধ্যমে ঘটনাগুলো ঘটলেই সেটাকে ধর্ষণ বলতে পারেন না। তাইলে আসলে ধর্ষণ কখন ঘটে? ধর্ষণ মূলত ঘটবে তখনই, যাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে সে যখন সেক্সুয়ালি ইন্টারকোর্সে রাজি না থাকা সত্ত্বেও এর বাইরে তার ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটা, সেটাই হচ্ছে ধর্ষণ। আর যৌনতা হচ্ছে সেই বিষয়টা, যেখানে দুইটা মানুষ তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে ঐক্যমতের ভিত্তিতে যৌনাঙ্গ ব্যবহার করে নানা ধরণের ইন্টারকোর্স ঘটান সেটা। যৌনতা আর ধর্ষণ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।
ধর্ষণ যৌনতার কোন ফর্ম না, যৌনতার কোন ধরণ না, যে ধরেন ধর্ষণ করার ভেতর দিয়ে কেউ সেক্সুয়াল প্লেজার পাচ্ছে– এটা ইম্পসিবল, এটা ঘটে না। তাহলে কী ঘটে? ধর্ষণ মূলত ক্ষমতার অপপ্রয়োগের একটা রাস্তার নাম। পৃথিবীতে ধর্ষণের ঘটনাটা তখনই ঘটে যখন যেই দু’পক্ষ একটা ঘটনায় জড়িত, একজন ভিক্টিম এবং যে ঘটনাটা ঘটাচ্ছে –এই দু’পক্ষের একপক্ষ রাজি না, কিন্তু সে অপর পক্ষকে প্রতিহত করতে পারতেছে না– কেবলমাত্র ঐধরনের সিচুয়েশনেই ধর্ষণের ঘটনাটা ঘটে। তার মানে ধর্ষণ যখন ঘটতেছে ঐমুহুর্তে মূলত একজন ধর্ষক সে গায়ের জোরে হউক বা অন্য কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা-বলে হউক, বা কোন পদের-বলে হউক বা সামাজিক অবস্থান-বলে হউক, সে আরেক জনের অমতকে উপেক্ষা করে সে ঘটনাটা ঘটাচ্ছে, মূলত ধর্ষণ তখনই ঘটে। এই ব্যাপারটাকে যদি আপনি ধর্ষণ বলেন, তাহলে আল্টিমেটলি ধর্ষণ আপনি ঠেকাবেন কীভাবে? ধর্ষণ ঠেকানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ব্যাপারটা হচ্ছে– এই যে ভিকটিম যে পক্ষটা আছে, যেকোন পরিস্থিতিতে সেই পক্ষটাকে ততটুকু পাওয়ারফুল রাখা বা তার হাতে ততটুকু পাওয়ার থাকা যেন তার একটা কথা যে সে রাজি না, এই কথাটুকুই এনাফ হয় অপরপক্ষকে আটকে দেওয়ার ব্যাপারে। অপরপক্ষ যেন আর এক চুলও না আগায় সেটা এনসিউর করতে পারবে জাস্ট একটা কথা, যে না এই কাজটা আমি করব না। এখানেই শেষ। এইটা ছাড়া অন্য যত আয়োজন আপনি করেন না কেন, যত ব্যাবস্থার কথা আপনি বলেন না কেন, কোনভাবেই ধর্ষণকে প্রতিহত করতে পারবেন না। তাইলে সেটা কীভাবে করা সম্ভব? যেমন ধরেন, আপনি একজন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক, আপনি জানেন এই জমিটা আপনার নিজের, এবারে আমি ঐ জমির মালিক না, কোন দিন যদি আমার মনে হয়, আমি আপনার ঐ জমিটাতে চাষাবাদ করব, আমি কেবলমাত্র তখনই ঐ সাহসটা করব, যখন আমার গায়ে জোর আছে। এমন জোর আছে যে, আমি রাষ্ট্রের লোকজন ম্যানেজ করতে পারব। যে আমি আপনার উপর জোর খাটাইলেও রাষ্ট্রের লোকজন কেউ আমাকে বাঁধা দিবে না। কেবলমাত্র তখনই আমি আপনার জমিটাতে গায়ের জোরে গিয়ে দখল বসাইতে পারব।
তাহলে রাষ্ট্র যদি এমন একটা আইনি কাঠামো রেডি রাখতো, এমন একটা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জারি রাখতে পারত, যে পরিস্থিতির মধ্যে কোন পক্ষ সে যত শক্তিশালীই হোক, হাজার চাইলেও সে আরেক পক্ষের জমিতে গিয়ে উঠতে পারবে না। উঠলে রাষ্ট্র তাকে পিটাইবে বা তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। মোদ্দাকথা উঠার আগেই রাষ্ট্র তাকে ঠেকাবে। দ্যাট ইজ দ্য কেইস। একইভাবে আমার শরীরও আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি! আমার নিজের সবচাইতে শেষ সম্বল বলি আর আশ্রয় বলি না কেন, সেটা আমার শরীর। সেই শরীরে কে ঢুকবে কে ঢুকবে না, কে হাত দিবে কে হাত দিবে না, এইটা হচ্ছে আমার সর্বশেষ সভ্রেন্টির জায়গা, সার্বভৌমত্বের জায়গা। ধরেন আমার বাড়ির মধ্যে আমি নিরাপদ, সেখানে আমি যেটা বলব সেটাই শেষ কথা। সেইম জিনিসটা আমার শরীরের প্রশ্নেও সমাজে জারি থাকতে হবে যে, আমার শরীরের প্রশ্নে আমি যা বলব সেটাই হবে শেষ কথা। আমার সাথে কে কী করবে, আমি কার সাথে কী করব না করব, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার একচ্ছত্র এখতিয়ার কেবলমাত্র আমার নিজের হাতে আছে। এই পরিস্থিতি বা ব্যবস্থায় যদি আপনি যাইতে না পারেন, তাইলে কোনভাবেই শরীরে অনধিকার প্রবেশ আপনি ঠেকাইতে পারবেন না। আর শরীরে অনধিকার প্রবেশ মানেই হচ্ছে ধর্ষণ।
তাহলে এটা কী ধরণের রাষ্ট্রীয় আয়োজনের মধ্য দিয়ে করা যায়? প্রথম কথা হচ্ছে, একজন নাগরিকের যে মর্যাদা, একজন ব্যক্তির যে মর্যাদা, সেইটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিতে হবে। সেটা কীরকম? ধরেন, নাগরিকের মর্যাদার মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে- কিছু বিশেষ ধরনের নাগরিক আইনের চোখে বিশেষ ধরনের সুবিধা পাবেন, আবার কিছু বিশেষ ধরনের নাগরিক তারা আইনের চোখে কম সুবিধা পাবেন। এইটা যদি একজন নাগরিকের অবস্থা হয়, তাইলে সেখানে দুইজন নাগরিকের মধ্যে সমানে সমানে সোশ্যাল ইন্টারেকশন হবে না। সেটা কীরকম? ধরেন, একজন ছেলের সামাজিক রাজনৈতিক আইনগত অধিকার বা মর্যাদা আর একজন মেয়ের সামাজিক রাজনৈতিক আইনগত অধিকার বা মর্যাদা এই দুইটা বাংলাদেশে ইক্যুয়াল না। একেবারেই ইক্যুয়াল না।
এই ইক্যুয়ালিটি যদি আপনি সমাজে আনতে চান, আপনাকে কী কী করতে হবে? প্রথমত, আইনের চোখে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নে, আয়-রোজগারের দিক থেকে, সন্তান গ্রহণ বা সন্তান গ্রহণ না করা সমস্ত দিক থেকে সমস্ত লিঙ্গের মানুষের সমান কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার থাকতে হবে। এবং সেই এখতিয়ারটা পুরা সমাজ এবং রাষ্ট্র সকল সদস্যের ঘাড়ে সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবে। মোদ্দাকথা, আপনার সমাজের প্রত্যেকটা সদস্যকে ইন্ডিভিজ্যুয়াল সিটিজেন হিসেবে রিকগনাইজ করতে হবে, একেক জনকে ব্যক্তিগত নাগরিক হিসেবে আপনার স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্রের জায়গা থেকে যদি আপনি কবুল না করেন তখন যেটা হবে- কে নাগরিক, কে নাগরিক না সেটার ব্যাপারে যদি আপনি সিলেক্টিভ থাকেন অথবা পুরা সমাজকেই যদি আপনি নাগরিক হিসেবে মেনে না নেন, আপনার সমাজে ব্যক্তি-ব্যক্তির যে সমতাটা, এক ব্যক্তির সাথে আরেক ব্যক্তির যে সাম্য, ইক্যুয়াল জায়গায় দাঁড়ানোর যে ঘটনাটা, এইটা আসলে হবে না। এই যে গভীর তাত্ত্বিক আলাপটা আমি করলাম, এটা আপনি আরও ভালো মতো বুঝবেন কীভাবে? ধরেন, ধর্ষণের স্বীকার যে শুধুমাত্র নারীরা হয় তা কিন্তু না, ধর্ষণের স্বীকার কিন্তু পুরুষও হয়। কিন্তু আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, পুরুষ-শিশুরা সবসময় ধর্ষণের শিকার হয়। যতগুলো ধর্ষণ-বলাৎকারের ঘটনা আপনি দেখবেন মাদ্রাসাগুলোতে, শিশুরা বাচ্চা শিশুরা ধর্ষণের শিকার হয়। কোনভাবেই একজন এডাল্ট হুজুর বা একজন এডাল্ট মানুষ আরেকজন এডাল্ট মানুষকে রেপ করতেছে এরকম ঘটনা আপনি খুব একটা বাংলাদেশে দেখবেন না। এই না যে বাংলাদেশের মানুষ খুব স্ট্রেইট, বাংলাদেশের মানুষ ছেলেরা ছেলেদেরকে রেপ করে না! ডেফিনেটলি করে। আপনারা প্রায়ই খবর পান যে মাদ্রাসায় বাচ্চাদেরকে রেপ করা হচ্ছে। কেন? কারণটা হচ্ছে, ঐ বাচ্চাটা সাবজুকেটেড সামওয়ান (subsucated someone) মানে হুজুরের উপর তার ভরণ-পোষণ, খাওয়া-দাওয়া, তার বেঁচে থাকা, তার টিকে থাকা, সবকিছু ডিপেন্ড করে। ফলে হুজুর বাচ্চাটাকে মনে করে সে তার ঘরের একটা পশু বা অন্য অনেকগুলো গৃহপালিত পশুর মধ্যে ঐ একটা। ফলে সে তাকে মনে চাইলেই রেপ করে। কিন্তু একজন হুজুর আরেকজন হুজুরকে জোর করে ধরে বেঁধে রেপ করে এমন ঘটনা আপনি পাবেন না। তার মানে, ব্যাপারটা কী? কেন পাবেন না? কারণ হচ্ছে ঐ দুইজন হুজুর কিন্তু সমান, আইনের চোখে বলেন সামাজিক ভাবে বলেন, তারা কিন্তু একজন আরেক জনের ইক্যুয়াল। ফলে তারা কোনভাবেই সেই চর্চাটা করতে পারেন না, কারণ তারা অলরেডি এগ্রি করে যে তারা দুইজন সমান। এবং তারা যে এগ্রিমেন্টে আসছে, তারা কিন্তু দুইজন বসে আলোচনা করে আসছে এমন না বরং সমাজ এবং রাষ্ট্র তার আইন দিয়ে, তার প্রথা দিয়ে, তার মূল্যবোধ দিয়ে এই দুইজনকে তার কর্তৃত্বটুকু দিছে যে, তোমরা দুইজন এডাল্ট এবং কর্তৃত্বের জায়গায় সমান। যে কারণে কখনোই এই দুইজন একজন আরেকজনকে রেপ করে না। কিন্তু যখনই এই কর্তৃত্বের প্রশ্নটা ক্ষমতার প্রশ্নটা অসমান হয়ে যায়, নারী আর পুরুষের প্রশ্নটা আসে, শিশু আর পুরুষের প্রশ্নটা আসে তখনই মূলত ধর্ষণের মতো জোরপূর্বক কারও শরীরে অনধিকার প্রবেশের ঘটনাটা ঘটে। তার মানে এখান থেকে এটা পরিষ্কার, যদি আমরা নারীকে কিংবা শিশুকে ঐ পুরুষের সমান জায়গায় নিয়ে আসতে পারি, তখনই কেবল ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। সেটা কীভাবে?
আজকের সমাজে আমাদের মূল্যবোধের জায়গায় বাচ্চাদের পেটানো জায়েজ আছে। বড়দের পেটানোর নিয়ম নাই। এইটা হচ্ছে বাচ্চার শরীরের উপর অনধিকার প্রবেশ, তার শরীরকে আপনি আঘাত করতে পারবেন, এটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং আইনগতভাবেও গ্রহণযোগ্য। আপনি আপনার বাচ্চাকে মারতে পারবেন, কিন্তু একজন এডাল্টকে আপনি মারতে পারবেন না। একজন এডাল্ট পুরুষকে আপনি মারতে পারবেন না, মারলে আপনার প্রতিক্রিয়া সহ্য করা লাগবে। মানে আপনাকে সে ফাইটব্যাক করবে। এই এগ্রিমেন্টে যে আসছে আপনার সোসাইটি, যে দুইটা এডাল্ট পুরুষ মানুষ একজন আরেকজনকে মারতে পারবে না। মারলে তার সমান প্রতিক্রিয়া তার সহ্য করা লাগবে। এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনাটাই মূলত একজন পুরুষকে ঐটুকু বাঁধা দেয় যেইটুকু বাঁধা দিলে একজন পুরুষ তার সহনাগরিক আরেকজন পুরুষের শরীরে অনধিকার প্রবেশের সাহস পান না। এখন এই বাঁধাটা সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক থেকে বাচ্চাদের বেলায় নাই, নারীদের বেলায় নাই। এটা না থাকার কারণে এরা দু’পক্ষই হয়ে গেছে প্রটেকশনলেস। তাদের কোন সেইফগার্ড নাই। সামাজিক মূল্যবোধের জায়গা থেকেও নাই, আইনের জায়গা থেকেও নাই, রাষ্ট্রের জায়গা থেকে রাজনৈতিকভাবেও নাই। এইটা হচ্ছে একটা সোসাইটিতে সব ধরনের নাগরিক – শিশু হউক, নারী শিশু হউক, পুরুষ শিশু হউক, নারী হউক, পুরুষ হউক, সকল নাগরিক যদি সমান হিসেবে পরিগনিত হয়, নাগরিক হিসেবে পরিগনিত হয়, শুধুমাত্র তখনই কারও শরীরে অনধিকার প্রবেশ করার এই জায়গাটা কমে আসে বা এই সুযোগটা কমে আসে। দ্যাট ইজ একচ্যুয়ালি রেপ বা ধর্ষণ, যেই জিনিসটা নিয়ে এতো বেশি আন্দোলন হচ্ছে।এই জায়গাটায় মনোযোগ দেওয়া খুব কঠিন, মানে এই জায়গাটায় কাজ করতে গেলে আমার সামাজিক কাঠামোয় বিশাল বড় পরিবর্তন আনতে হবে, আমার রাষ্ট্রীয় আইনে বিশাল বড় পরিবর্তন আনতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে আমার সম্পত্তির প্রশ্নে! আমাদের রাজনীতিবীদরা কোন দিন ঐ জায়গাগুলোতে যাইতে আগ্রহী না। বরং এই পুরা ব্যাপারাটাকে ব্যাবহার করে তারা আরও বেশি, আমাদের রাষ্ট্র আরও বেশি ধান্দা করতেছে যে কীভাবে আমাদের ঘাড়ের উপর আরও বেশি সাওয়ার হওয়া যায় বা আমাদের কতটুকু ধরে বেঁধে ফেলা যায়। সেটার লক্ষ্মণগুলো কী? ধরেন, রেপ সংক্রান্ত যা কিছু আলাপ আলোচনা আপনি দেখতে পাচ্ছেন গণপরিসরে বলেন, রাজনৈতিক পরিসরে বলেন সবই কিন্তু ‘একজন ধর্ষকের বিষয়ে রাষ্ট্র কী করবে’, -সেই সংক্রান্ত আলোচনা। মানে, ধর্ষণ অলরেডি সে করে ফেলছে, ঘটনাটা ঘটে গেছে! ঘটনা ঘটার পরে তার ব্যাপারে কী করা হবে? তাকে জনসম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হবে না কি নব্বই দিনে তার বিচার করতে হবে? এরকম নানান ধরনের কথাবার্তা। মানে একটা ঘটনা ঘটছে, মানুষ ভিক্টিম হইছে, যার ট্রমা পাওয়ার সে পাইছে, পাওয়ার পরে তারা এই ধরনের আলোচনা করছে।
এই ব্যাপারে যে প্রচলিত উদাহরণ আমাদের মোল্লারা দিয়ে থাকেন, ছাগল বা হরিণ বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াইলে তো বাঘ তাকে ধরে খাবেই! আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের মধ্যে এক পক্ষকে হরিণ বা ছাগল আরেক পক্ষকে বাঘ, এইটা বানানোর এখতিয়ার তোমাকে কে দিছে? কেন সব মানুষই বাঘ না? তাহলে বাঘে বাঘকে খাইতো না। মানুষকে ছাগল, ভেড়া, হরিণ এই লেভেলে নামিয়ে নিচ্ছে তারা এবং নিজেকে মনে করতেছে বাঘ। আসলে সে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। তো, এই যে আমাদের সোসাইটিতে একটা রিয়েলিটি বা আমাদের বোঝাপড়ায় ঐ জায়গায় যাওয়া যে নারী হউক, শিশু হউক, কেউ যাতে কাউকে কোন ভাবেই ছাগল বা হরিণের মতো ভক্ষণযোগ্য প্রাণী হিসেবে কন্সিডার করতে না পারে। আপনার রাষ্ট্রকে সেইখানে নিয়ে যেতে কাজ করতে হবে। সেইটা আপনি না করে আপনি নানান ধরনের আইনের সংস্কার, নানান দাবী-দাওয়া তুলতেছেন।
আসলে পরিবর্তনটা ঐ জায়গায় দরকার, যে সোসাইটির একপক্ষ নিজেকে হিংস্র বাঘ বা হায়েনা দাবি করে অন্য পক্ষকে ভক্ষণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করবে না। যেই সামাজিক পরিস্থিতিতে একজন নাগরিক আরেক জন নাগরিককে আক্রমণযোগ্য বা ভক্ষণযোগ্য প্রাণী হিসেবে কন্সিডার করতে পারে এবং নিজেকে হায়েনা জাতীয় কোন নৃশংস প্রাণী হিসেবে ভাবতে পারে এবং সেটাকে খুবই নরমাল হিসেবে দেখে- আপনার আইনগত সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো এনে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন যদি আপনি না ঘটাইতে পারেন, তাইলে ধর্ষণের মতো ঘটনা আপনি ঠেকাইতে পারবেন না। যে সোসাইটি অলরেডি এটা মনে করে নারী ভক্ষণযোগ্য, তাদের খাওয়া যায়, সেই সোসাইটির কাছে এই পুরো গোষ্ঠীটা অনিরাপদ। ফলে ঐ সামাজিক আইনগত পরিবর্তনটা ঘটাইতে হবে যেখানে গেলে আপনার নাগরিক, আপনি এবং আপনার সন্তান নিরাপদ। যেটা হচ্ছে গোড়ার কথা, সেই গোড়ায় আমাদের সোসাইটি যাচ্ছে না, না গিয়ে তারা আইন সংস্কার করবে। কী আইন সংস্কার করবে? একটা ঘটনা ঘটে গেছে, একজন ভিক্টিম আছে, সেই ভিক্টিমের জীবন কোথায় যাচ্ছে, না যাচ্ছে সেটা নিয়ে কারও কোন মাথা ব্যাথা নাই, মাথা ব্যাথা হচ্ছে- কী ধরনের আইন আমরা করব, যেটা দিয়ে ‘যেই অভিযুক্ত, সেই অভিযুক্তকে চেপে ধরা যায়’। এটার অনেকগুলো অ্যাস্পেক্ট আছে। ধরেন একজন লোক রেপিস্ট, তার নামে মামলা দেওয়া হয়েছে- ৯৫% রেপ কেইসে এই ব্যাপারগুলা পাবলিকলি আসে না। কারণ পাবলিকলি আসলে বাংলাদেশের সমাজ ব্যাবস্থায় ঐ মেয়েটার বিয়ে হবে না, পুরা পরিবার সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যাবে। তাকে বয়কট করা হবে, সোশ্যালি তাকে এক্সেপ্ট করা হবে না। যদি বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে এ ধরণের ঘটনাগুলো ঘটে তাহলে তার ডিভোর্সের সম্ভবনা আছে। ভবিষ্যতে সেই নারী কোথায় যাবে, বাচ্চাগুলো কীভাবে থাকবে- এই ধরনের নানান ধরনের কন্সিডারে জেনুইন রেপের ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আসে না। আবার ধরেন, ম্যারিইটাল রেপ যেগুলো- যেখানে বিয়ে করা বউয়ের উপর জোরপূর্বক যে ঘটনাগুলো ঘটানো হয়, সেগুলো নিয়ে খুব একটা আলোচনা বাংলাদেশের বাজারে হয় না।
কিন্তু বাংলাদেশে হাজার হাজার রেপ কেইস, প্রতিদিন অজস্র নারী নির্যাতন এবং রেপের মামলা বাজারে আসতেছে। এটার কারণ কী? এটার কারণ হচ্ছে – ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মামলাগুলো মিথ্যা/ভূয়া। কেন? কারণ যেহেতু রাষ্ট্র সমস্যার গোড়ায় সমাধান না করে, আইনের নানান ধরনের গ্যারাকল বানাইয়া ফেলছে, সেহেতু অনেক পক্ষই প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য এই গ্যারাকলগুলোকে ব্যাবহার করে। ফলে আপনি আপনার নাগরিকদের সামনে প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য নতুন কিছু গ্যারাকল এড করতেছেন। এটার যে সামাজিক পটভূমি, যে সামাজিক কনটেক্সটে একচ্যুয়াল রেপের ঘটনাগুলো সামনে আসতেছে না, পেছনে থাকতেছে। ফলে সমাজে ঘটমান হাজার হাজার রেপ প্রতিদিন আনপানিশড এবং আননোটিশ থাকতেছে। ফলে জিনিসটা যে করা যায়, এটা যে নরমাল, এটা যে সাধারণ একটা বিষয়, এটা সামাজিক পরিসরে মোটামুটি গৃহীত, এটার কোনো পরিবর্তন নাই। ফলে যে কেইসগুলো আসতেছে, মিথ্যা যেই কেইসগুলো আসতেছে, সেইটা কোন ভাবেই একচ্যুয়াল রেপ এর ঘটনা কোন ভাবেই কমাইতে পারতেছে না। কারণ একচ্যুয়াল রেপ এর কেইসগুলো তো সামনেই আসতেছে না। আর যেই মিথ্যা কেইসগুলো আসতেছে, সেগুলো দিয়ে মানুষকে নানান ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে, হয়রানি করা হচ্ছে। ফলে ধর্ষণের আইনগুলো যতবেশি কঠিন হবে, ততবশি মানুষকে ফাঁসানোর, মানুষকে আটকানোর, মানুষকে বিপদে ফেলার সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু একচ্যুয়াল যেই সমস্যাটা সেই সমস্যাটার আসলে কোন সমাধান হবে না। ধর্ষণের ঘটনার সমাধানে সমাজের ঐধরনের আইনগত সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পুন:গঠনের ওপর ডিপেন্ডেন্ট।
একটা মেয়ে কেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রেপ হওয়ার পরও মুখ খুলতে চায় না? কারণ হচ্ছে, সে যাবে কোথায়। সে পুরুষের অধীন, তার অনুগ্রহের দাসী–কোন না কোন পুরুষের। ধরেন, বাপ, নইলে জামাই, কোন না কোন পুরুষের সে অনুগ্রহের দাসী। এবং বাংলাদেশের সমাজে একটা মেয়ের জন্য সবচাইতে সেইফ হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য, স্বামীর দাসত্ব করা। বাপের দাসত্ব করা তার জন্য খুবই লজ্জাজনক, বাপের ফ্যামিলিতে ঝুলে থাকা তার জন্য খুবই অপমানজনক, নানান ধরনের গঞ্জনা তার উপর চাপানো হয়। সবচাইতে কম গঞ্জনার, কম অপমানের দাসত্ব বা গোলামী হচ্ছে জামাইয়ের গোলামী করা। ফলে ঐ সংসারটা আসলে সে ছাড়তে চায় না। তাই যত দিন যত বার এই ঘটনাটা ঘটতেছে সে আসলে মুখ খুলবে না। আবার কোন মানুষের কাছে যদি সে রেপ হয়, সেটা যদি তার সংসার জীবনকে বা দাসত্বকে বিপদের মুখে ফেলার সম্ভাবনা থাকে তখনও মূলত সে জিনিসটা হজম করে ফেলে।
তাহলে তাকে ঐ অবস্থান থেকে বের হইতে কী করতে হবে? প্রথমত, সে যে মানুষের অধীন হয়ে থাকছে, তাকে সেখান থেকে বের করতে হবে। তার মধ্যে ঐ কনফিডেন্সটুকু থাকতে হবে যে, তুমি কারও অনুগ্রহে না থেকেও এই সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবা। সেটা কীভাবে সম্ভব? পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার সমান অধিকার লাগবে, ঠিক তেমনি বিয়ের পর স্বামী- স্ত্রী যত সম্পত্তি বানাবে সব সমান সমান ভাগ হবে। সোজা হিসাব। যদি ঐটুকু ইক্যুয়ালিটি থাকে তার, তাইলে তার সারাজীবন ধরে কারও গলগ্রহ হয়ে থাকার বাস্তবতা থাকবে না এবং কেউ তাকে তার অধীন মনে করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, নিজেকে সিংহ অপর পক্ষকে ছাগল ভাবতে পারবে না। ফলে পরিবর্তনটা ওখানে লাগবে, ঐ ইক্যুয়ালিটিটুকু আমাদের এনসিউর করতে হবে। তা না করে, এই আইন টাইন সংস্কার করে আসলে খুব একটা লাভ নাই।
আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমাদের সমাজের জেনারেল পারসেপশনে কারও শরীরে অনধিকার প্রবেশ করা যায়, ঢোকা যায়, এটার আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে- আমাদের সোসাইটিতে যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাগুলো হচ্ছে, যে ধর্মীয় আলোচনা হচ্ছে, যে সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছে, সেই আলোচনায় নাগরিক ইন্ডিভিজ্যুয়াল এই কনসেপ্টগুলোর ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে । আপনি যদি আরবের সমাজের কথা চিন্তা করেন, দেখবেন আরবের সমাজে নারীর মতামতের কোন গুরুত্বই নাই, গ্রহণযোগ্যতাই নাই, তার মতামত দেওয়ার কোন জায়গাই নাই। যখন কোন মোল্লা আরব লিটারেচার থেকে আমাদেরকে মূল্যবোধ সংক্রান্ত কোন জ্ঞান দেয়, সে আসলে আগে থেকেই ধরে রাখে যে নারীর আসলে কোন এজেন্সি নাই, তার কোন এজেন্সি স্বীকার করা হবে না। এই যে নারীর এজেন্সি স্বীকার করা হবে না, আর যদি ধরে নেয় যে এটাই ন্যায়, এটাই ন্যায়সঙ্গত, তখন সে মূলত এই সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা যা-কিছু সে করে না কেন, সেখানে অলরেডি নারী নাই। যার শরীর অনুপস্থিত, চিন্তা ভাবনাতেও যার অ্যাকজিসটেন্সি নাই, তাহলে সে প্রাক্টিক্যাল কর্মকান্ডে কীভাবে অ্যাকজিস্ট করবে? ফলে সে আপনাকে যত ওয়াজ করবে, যত নসিহত করবে, তার সবই আসলে স্ববিরোধী একটা চাকা, যা চরকির মতো ঘরতে থাকবে।
ভিডিও থেকে ট্রান্সক্রিপশনঃ আশিক পারভেজ